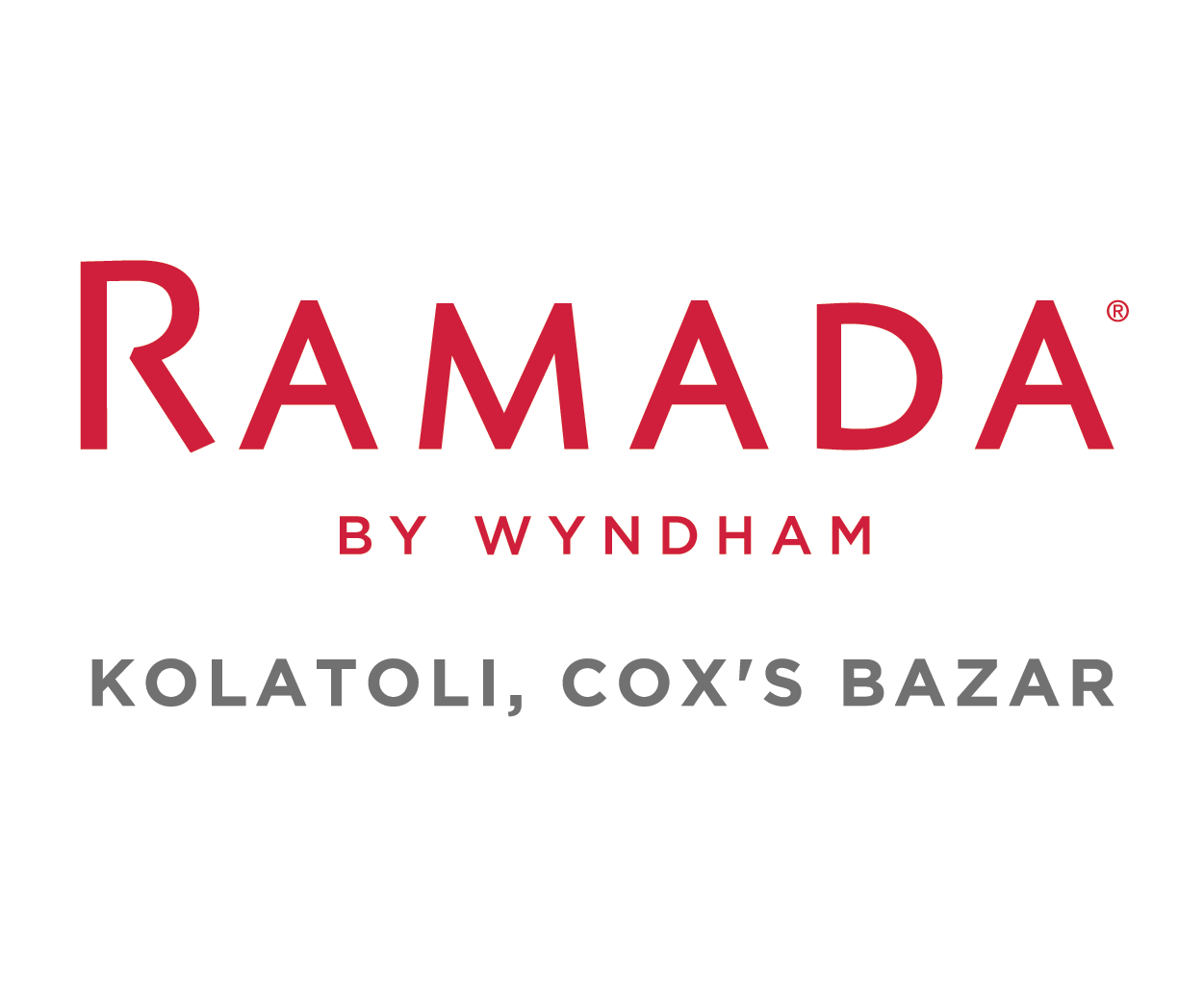মুক্তিযুদ্ধের জন্য আমরা মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম
সুলতানা কামাল
প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ০০:২৭ এএম
আপডেট : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ১১:০০ এএম

আইয়ুববিরোধী আন্দোলন যখন শুরু হলো; নারী আন্দোলনকে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এবং মূলধারার আইয়ুববিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে নারী আন্দোলনের কর্মীরা আমার মা সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন। এই পরিষদ বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ছোট ছোট কমিটির মাধ্যমে নারীদের ’৬৯-এর গণ-আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে।
’৬৯-এর গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুবশাহির পতন ঘটল। কিন্তু তিনি সুচতুরভাবে আরেক সামরিক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক চাপের মুখে ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বচন দিতে বাধ্য হলেন।
সত্তরের নির্বাচন হলো। নির্বাচনী রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী টালবাহানা শুরু করল। ক্ষমতা হস্তান্তর করবে নাÑ সেটা যখন বোঝা গেল তখন থেকে মা মহিলা সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে আন্দোলন করছিলেন। তারা পোস্টারে লিখেছিলেন, ‘গণ রায় বানচাল করা চলবে না’/ ‘ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে’ ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে বোঝা যাচ্ছিল- একটা সংঘাতের দিকে আমাদের যেতে হবে। এমন একটা অবস্থায় হয়তো গিয়ে আমরা দাঁড়াব যখন আমাদের একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো।
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমরা শুনলাম। মুক্তিযুদ্ধের ডাক শুনলাম। বঙ্গবন্ধু আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল’। এসবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা তখন থেকেই মোটামুটিভাবে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হই।
ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলন মানে- আমরা ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা বাদ দিয়ে মাঠে-ময়দানে ঘুরছি। মিটিং, মিছিল, পিকেটিং, নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিচ্ছি। আমাদের যে কাজগুলো করার, সেটা করে যাচ্ছি। ১৭ মার্চের দিকে স্বাধীনতা শব্দটির একেকটি শব্দ একেকজনের গলায় ঝুলিয়ে চারজন এ মিছিলের প্রথম সারিতে অবস্থান করি। পুরোভাগে আমার ছোট বোন সাঈদা কামাল (টুলু) এ মিছিল এগিয়ে নিয়ে যান। স্বাধীনতার ‘স্বা’ শব্দটি তার, ‘ধী’ শব্দটি শিল্পী সামিদা খাতুন, ‘ন’ শব্দটি শিল্পী পিনু খান এবং ‘তা’ শব্দটি ছিল আমার গলায়। এরও একটা কাহিনী আছে। এই মিছিলটি হওয়ার কথা ছিল চিত্রশিল্পীদের নিয়ে। এটা চারুকলা থেকে শুরু হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত যাবে। চারুকলা অনুষদকে তখন ইনস্টিটিউট বলা হতো। কারণ এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে তখনও যায়নি সেভাবে। পুরোনো নাম আর্ট কলেজও শোনা যেত অনেকের মুখে। সাঈদা যেহেতু আর্ট কলেজের ছাত্রী ছিল, তাই সে ওখানে গেছে। তখন ঝুঁকিপূর্ণ একটা পরিবেশ। সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। তারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছে। ও রকম একটা পরিস্থিতিতে ছোট বোনের সঙ্গে আমিও গেছি। যাওয়ার পর, স্বাধীনতার তিনটি অক্ষর যখন তিনজনে নিলÑ ‘তা’টা কে নেবে! অনেকেই সাহস করছিল না এ ব্যাপারে। ওখানে যারা অভিভাবকরা ছিলেন, তারাও দ্বিধান্বিত যে স্বাধীনতা লিখে শহরে যদি বের হয়Ñ এটার জন্য কোনোরকম রোষানলে পড়তে হয় কি না। আর্মি তো যেকোনো ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে।
চিত্রশিল্পী হাশেম খানের একটা লেখায় পেয়েছি; তখন আমি নাকি বলেছিলাম, ‘ঠিক আছে ‘তা’টা আমি নিলাম।’ তারপর স্বাধীনতা লেখা অক্ষরগুলো চারজনের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। সেটা নিয়ে আমরা মিছিল করে আর্ট কলেজ থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। অসহযোগ আন্দোলন মানে শুধু যে বর্জন করা বা কোনো কিছুতে যোগ না দেওয়া, সহযোগিতা না করা এমন না। এর সঙ্গে আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলাম, পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আমাদের থাকা সম্ভব নয়।
২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা শুরু হলো। এর প্রতিবাদে আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করলাম। মুক্তিবাহিনী গঠন করলাম এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। এটা এক দিনের ব্যাপার ছিল না। আমাদের মনে মনে একটা প্রস্তুতি ছিল এবং আমরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবÑ সেটার একটা ইঙ্গিত ছিল। এটা ঠিক, প্রথম দিকে একটু হতভম্বের মতোই ছিলাম। এই ধরনের কোনো আক্রমণ হবে, এটা আমাদের চিন্তায় ছিল না। রাজনীতিকরাও বুঝতে পেরেছিলেন কি না, জানি না। আমরা সাধারণ মানুষ তো বুঝতেই পারিনি।
২.
ধানমন্ডিতে তখন তেমন কোনো বাড়িঘর ছিল না। ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির সামনে লেকের ওপারে ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুল। তখন ওটা ছিল ওদিকের প্রথম ভবন। ২৫ মার্চের বিকালবেলায় আমাদের সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম। প্রতিদিন কিছু না কিছু একটা মিটিং হতো, মিছিল হচ্ছিল। সন্ধ্যায় সেখান থেকে যখন ফিরে আসছি দেখলাম, লেকের পাড় ধরে পাকিস্তানি সেনারা বন্দুক নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে তাক করে আছে। ব্রিজ পর্যন্ত, লেকের ওই পাড় থেকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে তাক করা। ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুলের ছাদে পাকিস্তানি সেনারা বন্দুকসহ অবস্থান নিয়ে আছে। এটা দেখে আমি সাঈদাকে বললাম, এত পাকিস্তানি সেনা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ওরা কি বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলার তাল করছে? কত মানুষকে ওরা মারবে? তখন মনে হয়েছে, এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার! এত মানুষকে মারতে চায় ওরা। এটা কি সম্ভব? বাসায় চলে এলাম। রাত বারোটার দিকে আমার ভগ্নিপতি ফোন করেন। তিনি চট্টগ্রাম বেতারে ছিলেন। আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মার কথা জিজ্ঞেস করলেন। মা কেমন আছেন? আমাদের কী অবস্থা। মা কোথায়? আমি বললাম, মা বাড়িতে আছেন। আমরা ভালো আছি। তিনি বললেন, ‘অবস্থা ভালো না’। কথা বলতে বলতে লাইনটা কেটে গেল। এরপর আর টেলিফোনে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা গেল না। এর কয়েক মিনিট পরই আমরা গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। মূলত মেশিনগানের শব্দ। মানুষের কোনো চেঁচামেচি নেই। তবে কিছু মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে, সেটা টের পেলাম। বাড়িঘর কম থাকায় শব্দ চলে আসত। মনে হলো, ব্রিজের ওপরে হয়তো কাউকে গুলি করে মারা হলো। ব্রিজের ওপরে পায়ের শব্দ, তারপর গুলির শব্দ। লোকটা পড়ে গেলÑ এ রকমই মনে হলো। আমরা দৌড়ে গেটের কাছে গেছি। আমাদের বাড়ির গেট এত বড় ছিল না। ছোট দেয়াল ছিল। গেটের কাছে উঁকি দিয়ে দেখি, দাউ দাউ করে ওদিকে আগুন জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে। আমাদের পাশের বাড়িটা ছিল একতলা। ওরা ইকবাল হলের দিকে দেখিয়ে বলল, ওই দিকে আগুন জ্বলছে। এদিক থেকে কোনাকুনিভাবে আমরাও আগুন দেখতে পেলাম। আগুনের ধোঁয়া উঠছে এবং আগুন দেখা যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারলাম, বড় কোনো ঘটনা ঘটে গেছে। কয়েক ঘণ্টা আমাদের হতভম্বের মতো গেল। শেষ পর্যন্ত রেডিওতে শুনলাম, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেটা নিয়েও মানুষের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। আসলে কী হয়েছে? তিনি এখনও বেঁচে আছেন নাকি বেঁচে নেই- এ রকম নানা দোলাচল।
২৫ থেকে ২৭ মার্চ রাত পর্যন্ত কারফিউ দেওয়া হলো। টেলিফোন বন্ধ। কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। ২৭ মার্চ দুপুর থেকে আমাদের কিছুটা যোগাযোগ শুরু হলো। আমাদের সঙ্গে যারা বিভিন্নভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের সঙ্গেÑ শাহাদত চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র-বন্ধুÑ তারাও যোগাযোগ করলেন। তাদের জানালাম, ৩২ নম্বরের ব্রিজের ওপর ডিসি পানাউল্লাহর ছেলে খোকনের লাশ পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে আরও তিনজন ছেলে ছিল। তাদের হাতে রাইফেল ছিল। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির সামনে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শাহাদত চৌধুরী জানালেন, হাটখোলা থেকে আমাদের বাড়ির পথে অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জিসি দেবের লাশ, ছাত্রছাত্রীদের লাশ দেখেছেন। তিনি চিলেকোঠা থেকে ভিস্তিওয়ালা উত্তমের লাশও দেখেছেন।
৩.
কবি সুফিয়া কামালের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িটি মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দুর্গ হয়ে উঠল। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতে থাকল। এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না। এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। কারণ প্রতিদিন মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা যেখানে আছেন সবাইকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। নারায়ণগঞ্জের সাত্তার জুট মিলসে আমাদের আত্মীয় পরিবারের সদস্যদের ব্রাশফায়ার করে মারা হয়েছে। শিশু সন্তানসহ মা ঘুমিয়ে ছিলেন। তাদের মারা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের হত্যার কথাও শুনলাম। অন্য যাদের হত্যা করা হয়েছে অনেকের নাম শুনেছি। নাম না-জানা প্রচুর মানুষকে মারা হয়েছে। ইত্তেফাক অফিসের সামনে যাত্রীসহ রিকশাওয়ালাকে হত্যা করা হয়েছে।
কাছাকাছি আমাদের যে বন্ধুবান্ধব থাকত তারা এলো। আমরা নিজেরা কীভাবে সংগঠিত হতে পারি, কী করতে পারিÑ আলোচনা করছি। প্রথমদিকে যারা পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর অত্যাচারে শহীদ হয়েছে, তাদের পরিবারকে কোনোভাবে সাহায্য করা যায় কি না, এমন আলোচনাও করেছি।
এপ্রিলের দিকে আমরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করি। শুরু করি খবর আদান-প্রদান করা দিয়ে। কোনো বন্ধুকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া। তাদের আশ্রয় দেওয়া। একটা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাসাটা মোটামুটি নিরাপদ ছিল। কলকাতা বেতার থেকে প্রচার হলোÑ ‘ওরা কবি সুফিয়া কামালকে হত্যা করেছে’। এই খবরে বিদেশি দূতাবাসগুলো পাকিস্তানকে চাপ দিল। সত্য কী জানতে চাইল। পাকিস্তান রেডিও-টেলিভিশনের কর্মকর্তারা দৌড়ে এলেন ক্রুদের নিয়ে আমাদের বাড়ি। সৈয়দ জিল্লুর রহমান তখন ঢাকা রেডিওর আঞ্চলিক পরিচালক। তার সঙ্গে এলেন কবি হেমায়েত উদ্দিন আহমদ। বারান্দায় বসে মা তাদের বললেন, ‘সাক্ষাৎকারের কী আছে। দেখেই তো গেলেন আমি বেঁচে আছি। একে যদি বেঁচে থাকা বলে তবে বেঁচে আছি!’ হেমায়েত উদ্দিন আহমদ টেপ বন্ধ করে বললেন, ‘খালা, আপনি এভাবে বলবেন না, আপনার ক্ষতি হতে পারে।’ মা থামলেন না। বললেন, ‘আমাদের ছেলেরা যুদ্ধে যাচ্ছে, রাস্তায় গুলি খেয়ে মরছে, ছোট মেয়ে কবি মেহেরুনকে ওরা মেরে ফেলেছে, এভাবে বেঁচে থাকার কী মানে আছে...।’ ‘আমি বেঁচে আছি।’ সেটার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার যেটা করেছিল; তাকে দিয়েই বলানোর চেষ্টা করছিল, এই যে বলা হচ্ছে মানুষ মারা হচ্ছে। এটা সত্যি না। সুফিয়া কামাল জীবিত আছেন। বিভিন্ন দূতাবাসে, টিভি ক্যামেরায় মায়ের ছবি তুলে পাঠানো হলো। অর্থাৎ, মাকে বাঁচিয়ে রাখা তখন একটা দায়িত্ব পাকিস্তান সরকারের। তা ছাড়া আমাদের বাড়ির পেছনে ছিল সোভিয়েত দূতাবাসের অফিস। তারা আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখত সম্ভবত। সেজন্য আমাদের বাড়িতে কোনো আক্রমণ হয়নি। সে কারণেই বন্ধুবান্ধবরা আমাদের বাড়িতে এসে নিশ্চিন্তে মিটিং করত। কথাবার্তা বলত। ক্রমশ সুফিয়া কামালের বাড়িটা মুক্তিযুদ্ধের একটা কেন্দ্রে পরিণত হয়।
এই পরিস্থিতিতে এপ্রিল এবং মে গেল। আমরা লোকজনকে নানাভাবে সহযোগিতা করছি। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতিবেশী স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহকে সীমান্ত অতিক্রমে সহযোগিতা করেছিলাম। তার পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নিই। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে হলো, আমরা সীমান্ত পার হব। শাহাদত চৌধুরীর সহযোগিতায় ঢাকার এক গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার সঙ্গে আমরা দুই বোন, মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদুর রহমান বেনু, মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী, আমাদের আরেক বন্ধু মিলিয়া, বন্ধু নাসরীন আহমাদ, হামিদুল্লাহ ভাইয়ের পরিবার অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, তিন ছেলেসহ গেছেন। ঢাকা থেকে কুমিল্লা, সেখানে চান্দিনা বাজারে নেমে আমাদের কয়েকটা রিকশা নিয়ে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে যেতে হয়েছে। গ্রামগুলোর নাম বলতে পারব না, সবগুলোর নাম জানা ছিল না। গ্রামের পথ ধরে ত্রিপুরার সোনামুড়া যাই। আমরা ঠিক করেই গিয়েছিলাম, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। আমাদের বাবা খুব মন খারাপ করেছিলেন। দুই মেয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? ফিরে আসবে কি না। তিনি শুধু একটা কথা বললেন, যাবে যদি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে পারলেই যেও। শুধু জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যেও না।
৪.
১৬ জুন ১৯৭১, শ্রীমন্তপুর চেকপোস্টে পৌঁছাই। আমাদের সঙ্গে স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহর পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন। সোনামুড়া থেকে শ্রীমন্তপুর চেকপোস্টের দূরত্ব প্রায় তিন মাইলের মতো। সোনামুড়ায় আমাদের পরিচিত একজন ডাক্তার ছিলেন- ডা. ক্যাপ্টেন আখতার আহমেদ। আখতার ভাইয়ের গল্পটা মজার। তিনি পাকিস্তান আর্মি মেডিকেল কোরের সদ্য কমিশন পাওয়া অফিসার। আর্মি মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছেন ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে। একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাতের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের গুলি করছে, তখন তিনি মেডিকেল সেন্টারে ছিলেন। গুলির খবর পেয়ে তিনি হাসপাতাল থেকে যতটা পারেন ওষুধপথ্য, ব্যান্ডেজ, অপারেশনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি একটা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেন। নিজেই অ্যাম্বুলেন্স চালিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে চলে যান ত্রিপুরা রাজ্যে। ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন খালেদ মোশাররফ। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আখতার ভাই একটা মেডিকেল সেন্টার চালানোর অনুমতি পান।
আখতার ভাই প্রথমে শ্রীমন্তপুর পরে ২ নম্বর সেক্টরে চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। চিকিৎসাসেবা কক্ষ করার কোনো খালি জায়গা ছিল না। পাশে একটি গোয়ালঘরকে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে ঠিক করা হয়। মেঝে ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। এক পাশে রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য টেবিল কাম বেড, আরেক পাশে মেডিসিনের ওয়ার্ডরোপ রাখার ব্যবস্থা। কিন্তু রোগীর বেড না থাকায় চারটে ইট চার কোনায় পেতে কয়েকটা কাঠের তক্তা বিছিয়ে রোগীর শয্যা আর এক পাশে ওই রকম তক্তা বিছিয়ে ওষুধ, ইনজেকশন, গজ, ব্যান্ডেজ সরঞ্জামাদি রাখার ব্যবস্থা করলেন আখতার ভাই। এর পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গ্রামের পশ্চিম সীমানা বরাবর। রাস্তার ও পাশে একটি মসজিদ ছাড়া আর কোনো বাড়িঘর নেই। একাত্তরের ৯ মে বিবির বাজার যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই হাসপাতাল পর্ব শেষ হয়ে যায়। হাসপাতাল স্থানান্তরিত হয় সোনামুড়ায়। এখানে তার সঙ্গে যোগ দেন নার্সিং সুবেদার মান্নান (এএমসি)। সঙ্গে আরও কয়েকজন মেডিকেল কোরের সদস্য ছিলেন। ফরেস্ট বাংলো অফিসারের সঙ্গে আখতার ভাইয়ের দেখা হলে তিনি সব খুলে বলেন। তাকে ফরেস্ট বাংলোর দুটো কক্ষ দেওয়া হয়। ত্রিপুরার কনজারভেটর অব ফরেস্ট নরেশ ভট্টাচার্য রেস্ট হাউসের একটি ঘর, ফরেস্ট অফিসের একটা টিনের ঘর দেন রোগী রাখা ও রোগী দেখার জন্য। অ্যাম্বুলেন্সেও মেডিকেলের কাজ করা হতো। এখানে আহতরাও চিকিৎসাসেবা নিতে আসতেন।
আমরা যেহেতু আখতার ভাইকে চিনতাম তাই তাকে গিয়ে বললাম, আমরা কলকাতায় যাব না; আপনার কাছে থাকব। আখতার ভাই বললেন, আজকের রাতটা এখানে থাকো। দেখি কী করা যায়! তিনি সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। রেস্ট হাউসের রুমগুলো ব্যবহারের অনুমতি ছিল না। শেষমেশ আখতার ভাই হামিদুল্লাহর স্ত্রী, বাচ্চা ও আমাদের একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করলেন। ছেলেদের জন্য বারান্দায় রাত কাটানোর ব্যবস্থা হলো। এর মধ্যে হঠাৎ নরেশ ভট্টাচার্য এসে বললেন, কী হচ্ছে? তাকে সামাল দিলেন আখতার ভাই।
পরদিন অন্যরা কলকাতা চলে গেল। আমরা দুই বোন থেকে গেলাম। সন্ধ্যায় ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এলে আখতার ভাই আমাদের দিয়ে নার্সিং চালু করলে কেমন হয় জানতে চাইলেন। প্রস্তাবটা খালেদ মোশাররফের পছন্দ হলো। তিনি অনুমতি দিলেন। ঢাকা থেকে আরও মেয়েরা আসতে চাইলে তাদের উৎসাহ দিতে বললেন।
এইচ টি ইমাম আগরতলায় বাংলাদেশ সরকারের হয়ে কাজ করছিলেন। বাংলাদেশ থেকে যারা নানাভাবে যাচ্ছেন, শরণার্থী হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব তার ছিল। আমরা তার সঙ্গে দেখা করি। ২০ জুন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হলো। আমাদের একটা নম্বর হলো, রেশনের অর্ডার হলো। এর আগে আমরা অন্যদের খাবার ভাগ করে খাচ্ছিলাম।
৫.
আমরা দুই বোন হাসপাতালে যোগ দেওয়ার পর এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। আমরা হাতেকলমে নার্সিংয়ের কাজ শিখতে লাগলাম। রোগীর জ্বর দেখা, ইনজেকশন দেওয়া, ক্ষত পরিষ্কার করা, ড্রেসিং করা সব শিখে নিলাম। ওষুধপথ্যের পাশাপাশি স্নেহ-মমতা দিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। হাসপাতালে অনেক রকম রোগী আসত। বেশিরভাগই বুলেট ইনজুরি। বুলেট বেরিয়ে গেলে রক্ত বন্ধ করা আর ইনফেকশন চেক করতেন ডাক্তাররা। শেল আর মর্টার, মাইন ইনজুরির রোগীরাও আসতেন। এমনও কেস আসত আহত হননি, গোলার শব্দে কানে তালা লেগে গেছে। কথা বন্ধ হয়ে একেবারে শকে চলে গেছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য অ্যালার্জিজনিত সমস্যার রোগীও আসত। বাংলাদেশের কোনো এক গ্রাম থেকে একদিন একজন রোগী আনা হয়েছিল। হাত, পা, মুখে গুলি লেগেছে। মুখের গুলিটা এক পাশের চোয়ালের অনেকটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লাইন দিয়ে গুলি করে ফেলে চলে গিয়েছিল। পালিয়ে যাওয়া গ্রামবাসীরা ফিরে এসে ওকে জীবন্ত পেয়ে এখানে পাঠিয়ে দেয়। অপারেশন করার সময় টুলু টর্চ ধরে। ক্যাপ্টেন ডা. আখতার ভাই অপারেশন করলেন। সুবেদার মান্নান সব রেডি করে দিয়েছিলেন। অপারেশন শেষ করতে করতে ভোর হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রোগীটা বেঁচে যান।
এর মধ্যে ঢাকা থেকে মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারে এমবিবিএসের ছাত্র শামসুদ্দিন ও সবিতা এলেন। তাদের সঙ্গে এলো ডালিয়াও। ডালিয়া যদিও মেডিকেলের ছাত্রী ছিল তবু সে আমাদের সঙ্গে নার্সিং ব্রিগেডে যোগ দেয়। আমাদের এবার দুজন ডাক্তার আখতার ভাই ও শামসুদ্দিন, তিনজন নার্স টুলু, ডালিয়া আর আমি এবং সুবেদার মান্নানসহ মেডিকেল কোরের বেশ কয়েকজন লোক। ফরেস্ট বিভাগের দৌলতে থাকার ব্যবস্থা তো রয়েছেই। হেডকোয়ার্টার থেকে সেনাবাহিনীর নিয়মমাফিক রেশন ইত্যাদি পেতাম। আমাদের জন্য রান্না করত বাংলাদেশ থেকে আসা মুনির নামে একটি ছেলে। ও রোগীদের রান্নাও করত। রান্নার হাত ভালোই ছিল। রেডক্রসের প্রজেক্ট থেকে আমাদের বেতনের ব্যবস্থা করে দিলেন আগরতলা হাসপাতালের সার্জন ডক্টর রয় চৌধুরী। এসব হলেও মেডিকেল রসদ অর্থাৎ ওষুধপথ্য, যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্টস, অপারেশন টেবিলÑ চিকিৎসাসেবার জন্য প্রয়োজনীয় এই জিনিসগুলোর অভাব রয়েই গেল। আখতার ভাইয়ের স্ত্রী খুকু সোনামুড়ায় এলেন জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। রেডক্রসের সেই প্রজেক্ট থেকে খুকুর জন্যও বেতনের ব্যবস্থা করে দিলেন ডক্টর রয় চৌধুরী। খুকু যোগ দেওয়ায় আমাদের দুটি শিফট করা হলো। খুকু আর আমি পার্টনার। ডালিয়া আর টুলু পার্টনার। টুলু আর ডালিয়া মেডিকেল দিকটা দেখত। আমি আর খুকু সার্জিক্যাল দিকটা দেখতাম। ইনজেকশন দেওয়া, অপারেশন হলে তাতে সহযোগিতা করা। আমাদের তো নার্সিং ট্রেনিং ছিল না। হাতেকলমে কাজই ছিল ভরসা। (অংশবিশেষ)
লেখক : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মানবাধিকারকর্মী