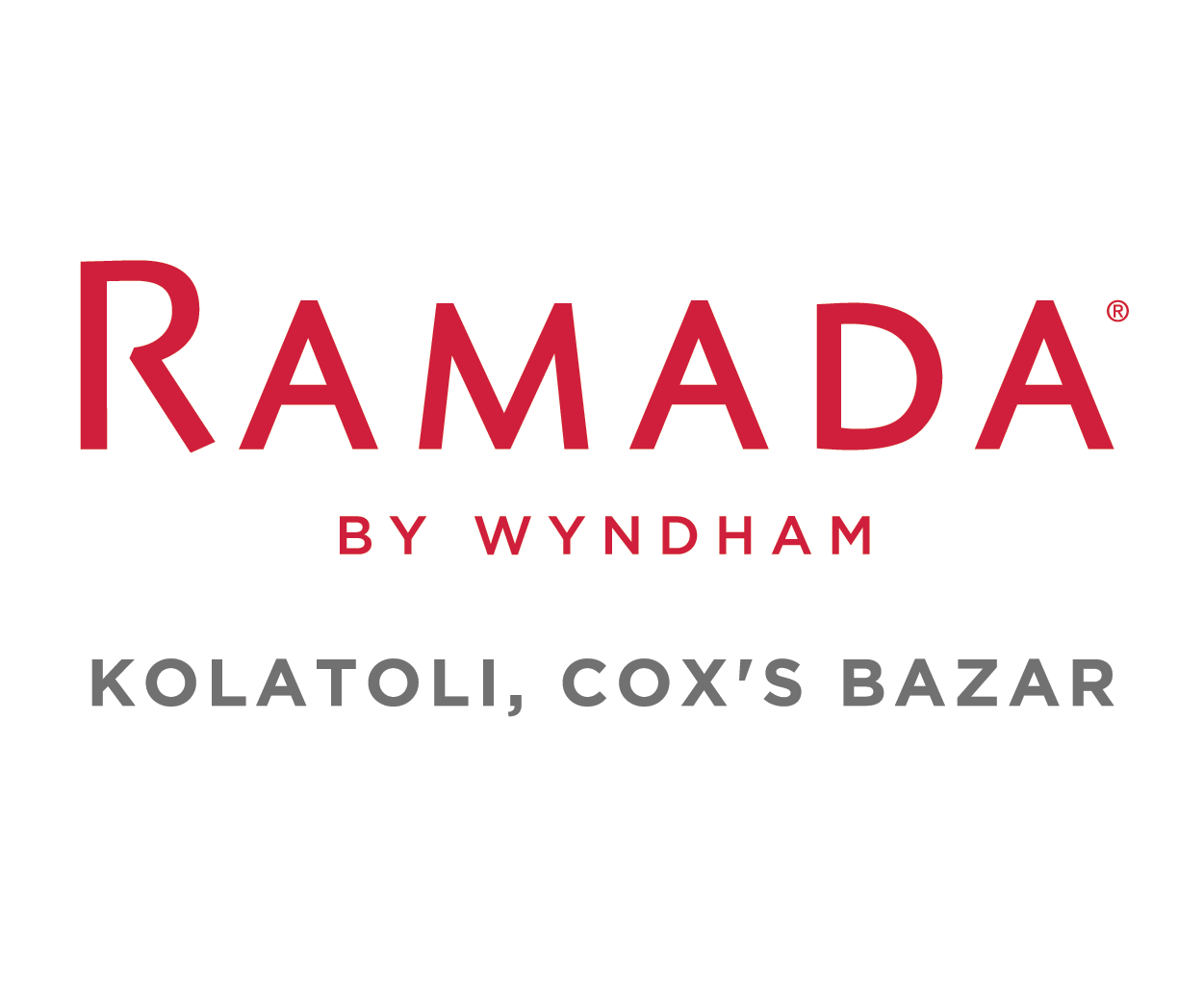প্রগতিশীল সব শক্তির ঐক্য খুব জরুরি
নাসির উদ্দীন ইউসুফ
প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ০০:২৩ এএম
আপডেট : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ১১:০০ এএম

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের মানুষের স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্য বা চারিত্রিক গুণ রয়েছে। এ দেশের মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকাংশ আন্দোলনের রূপরেখা আগে থেকে কেউ দেয়নি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের কথাই ধরা যাক। এর আগে ধর্মের ভিত্তিতে দুটি দেশ সৃষ্টি হয়। মুষ্টিমেয় কজন দেশভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ কৃত্রিম প্রচেষ্টা স্বতঃস্ফূর্ত কিছু ছিল না। দেশভাগ অনেকটা দেহকে দুই টুকরো করে দেওয়ার মতোই মর্মন্তুদ ঘটনা ছিল। ওই বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বায়ান্নতে। ভাষা ও সংস্কৃতি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে পৃথিবীর সবখানেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। অপ্রাপ্তির নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় মানুষ। একাত্তরে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শুরু মার্চে; যা পূর্ণতা পেয়েছিল ডিসেম্বরে। রক্তস্নাত মাটিতে অর্জিত হয়েছিল লাল-সবুজের পতাকা। বিজয়ের আনন্দে নতুন করে দেশ পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখা শুরু করে মানুষ। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ফিরে আসেন স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় পরপরই।
ফিরে তাকাই পেছনে। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় সোনার বাংলা গড়ে তোলার নতুন প্রচেষ্টা। সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেকোনো দেশের জন্য এমন ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথা। কিন্তু ইয়াহিয়া খান একবারও আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেননি। তার ওই নির্লিপ্ততায় গোটা দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়ে ওঠার পেছনে ঐতিহাসিকভাবে বাঙালির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবহেলা প্রদর্শন, বৈষম্য প্রভাব রেখেছে। সত্তরের ওই সময়ই সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের ক্ষোভ ছিল। সামনে নির্বাচন। আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে জবাব দেব। নির্বাচনে সাধারণ মানুষের মতামতই প্রাধান্য পেয়েছে। ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়ী হয় আওয়ামী লীগ। বাঙালি বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে সহাবস্থান এক প্রকার অসম্ভব হয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের অসহযোগিতার দরুন একসময় আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়তে হয়। সে যুদ্ধ হয়েছিল জনযুদ্ধ। দেশ মুক্ত করার তাগিদ অনুভব করে অনেকে নেমেছিল যুদ্ধের ময়দানে। শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ।
একাত্তরের আগে থেকেই আন্দোলন আমায় টানত। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলাম, সেখান থেকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হতো। আমার মনে হয় ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানই কিন্তু আমাদের বাঙালি হিসেবে নিজেদের আবিষ্কার করার একটা প্রবণতা তৈরি করেছিল। তারপর আর আসলে ঘরে ফিরতে ইচ্ছা হয়নি। মিটিংয়ে বক্তৃতা না করলেও কবিতা আবৃত্তি করতাম। ১৯৬০-এ হলো রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আর ১৯৬৪-তে শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল এবং আমার মনে আছে আমি পুলিশের মার খেয়েছিলাম। সে সময়ই আমি শেখ মুজিবকে প্রথমবারের মতো নেতা হিসেবে বুঝলাম। তিনি সারা দেশে মিটিং করছেন, পত্রিকায় পড়ছি। আমার মনে হয় তিনি কিন্তু পশ্চিমা বুর্জোয়াদের শোষণটাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, যতটা না পেরেছিলেন কমিউনিস্টরা। এর ফলেই কিন্তু ১৯৬৬-এর ছয় দফাটা তিনি স্ট্রংলি তুলতে পেরেছিলেন। দেশের মানুষও তার এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিল বলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি সবার আস্থা ছিল প্রগাঢ়। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কালরাতে আমি রাস্তায়। হামলার সময় নিজ চোখে সব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ থেকে আগেই সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, যার যার এলাকায় যেন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তো নির্দেশনা আগে থেকেই দেওয়া ছিল। কাকরাইলের জোনাকির রাস্তায় তখন সংস্কারকাজ চলছিল। অধিকাংশ শ্রমিকই নোয়াখালী থেকে এসেছিলেন। শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের তত দিনে চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল। আমরা প্রায়ই ওই রাস্তা দিয়ে মিছিল করে যেতাম। এভাবেই তাদের সঙ্গে পরিচয়। আমরা কজন তখন ওদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করি গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করে ফেলা হবে। ঢাকা তখন খুব সুন্দর প্রাকৃতিক শহর ছিল। রাস্তার ধারের সুন্দর ওই গাছগুলো কাটার সময় কিছুটা মন খারাপ হচ্ছিল। একসময় আশপাশের অনেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। দিনমজুররা তো রয়েছেই। একে একে চায়ের দোকানের মেসিয়ার, স্থানীয় দোকানদার ও তরুণরাও যুক্ত হলো। হাজার হাজার মানুষ গাছ কেটে রাস্তায় ফেলছে। শুরুতে জায়গাটিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থাৎ আমরা কয়েকজন ছাত্রনেতা ছিলাম। কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আমরা আর পাত্তাই পাচ্ছিলাম না। অনেক বাড়ি থেকে নারীরাও নেমে এসেছিল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে।
পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকা শহর মানুষের অবস্থানে অবিশ্বাস্য এক রূপ নিয়েছিল। ফার্মগেট থেকে শুরু করে গোটা ঢাকায় লক্ষাধিক মানুষ রাস্তায় অবস্থান করছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকায় হামলা করছে। ভয়াবহ ওই রাতে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে হলেও অনেক মানুষ একত্র হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। অদ্ভুত বিষয়! এ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্ব ছিল না। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল একতা। কাকরাইল মোড়ে সেন্ট্রাল চার্চের সামনে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এসে পৌঁছায় ততক্ষণে ঢাকার ওই অংশে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্যাংকগুলো আবছা দেখা যাচ্ছিল। বড় বড় গাছের আড়ালে আমরা শুয়ে আছি। অন্ধকারে গাড়ি চলাচলের শব্দ পাচ্ছি। পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহনগুলোর বাতি নেভানো। তাই আমাদের পক্ষে ঠাওর করা কঠিন কী হচ্ছে। অনেকক্ষণ রাস্তায় থাকায় আমরা তখনও জানতে পারিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। আমাদের সম্বল বেতের সুটকেসে ১০টি হাতবোমা আর আমার এক বন্ধুর হাতে পিস্তল। পাকিস্তানি সেনারা প্রথম কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গেই মাটি কেঁপে ওঠে। আমরা তখনও বুঝিনি ওরা হামলা শুরু করে দিয়েছে। কামান দেগে রাস্তায় বিছিয়ে রাখা গাছগুলো ওড়া উড়িয়ে দিচ্ছিল। এমনকি রাস্তায় ফেলা মোটা আরসিসি পাইপগুলো ভেঙে ওরা ফকিরাপুলের দিকে এগিয়ে চলে। উপায়ান্তর না দেখে আমরা সরে পড়ি।
সেদিন আমাদের প্রতিরোধ পনেরো মিনিটের বেশি টেকেনি। আমরা এক বাড়ির ছাদে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ শুরু করি। পাকিস্তানি সেনাদের ট্যাংক সব বাধা গুঁড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু পর রাজারবাগে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ। বুঝতে পারলাম পুলিশ লাইনস আক্রান্ত হয়েছে। আস্তে আস্তে আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখি। বুঝতে পারি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পঁচিশে মার্চ কালরাতে জনগণের এ প্রতিরোধটুকুর গুরুত্ব কম নয়। সারা রাত ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছে। সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে তাদের প্রতিরোধ স্থায়ী হয়নি। কিন্তু মানুষ ঐক্যবদ্ধ ছিল। প্রতিরোধের এ তীব্রতা সেদিন পাকিস্তানি সেনারাও বুঝতে পেরেছিল। বুঝেছিল বলেই তারা আরও আগ্রাসি হয়ে উঠেছিল। পঁচিশে মার্চের নির্মমতার সাক্ষী অনেকেই হয়তো ভেবেছিল এ যুদ্ধে বিজয় অসম্ভব। কিন্তু মানুষের মধ্যে একতা আর দুর্বিনীত হওয়ার প্রবণতার কারণে যুদ্ধ বরণ করে নেওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। ছাব্বিশ মার্চ দিবাগত রাতে ইপিআরে পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র প্রতিরোধটিও মুক্তিযুদ্ধের জন্য জরুরি ছিল। ২৭ মার্চের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। ওইদিন চার ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি করা হয়। ইপিআরে পুলিশের ফেলে যাওয়া অস্ত্র সাধারণ মানুষ সংগ্রহ শুরু করে। আমরা ছাত্রনেতারা তখনও ঢাকায়। মানুষ এসে আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল। অর্থাৎ প্রবল আক্রমণের মুখেও মানুষ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেনি। পরাধীনতার যন্ত্রণা তাদের কুরে কুরে খাচ্ছিল। ওই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনায় গোটা দেশ একজোট হয়েছিল।
গোটা মুক্তিযুদ্ধ পর্ব ছিল একতার। গোটা জাতি একত্র হয়ে অসম সাহসী লড়াই চালিয়েছিল। যুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলেও প্রত্যেকের ছিল স্বকীয় ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনগণের যুদ্ধ। প্রথম থেকেই তা ছিল জনযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ পর্বের প্রথমে প্রাণ দিয়েছিল সাধারণ মানুষ। পঁচিশে মার্চে মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। এ প্রেক্ষাপটের মাধ্যমের জনগণের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই আমরা মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু এবার মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠার বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় একতার বিস্ফোরক বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে লড়াইয়ের যে মঞ্চ গড়ে ওঠে, সেখানে একে একে যুক্ত হতে শুরু করে আরও অনেকেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই জাতিগত ঐক্য আমাদের পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে সমন্বয়, ব্যবস্থা ও সুসংগঠিত করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। জাতীয় ঐক্য না থাকলে সুপ্রশিক্ষিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হতো না।
মুক্তিযুদ্ধ শুরু থেকেই জনযুদ্ধ হওয়ায় দীর্ঘ নয় মাস আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পেরেছি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলাম আমরা। দেশ মুক্ত করার লক্ষ্যে অবিচল। এ সময় জাতীয় ঐক্য মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা জুগিয়েছে। পঁচিশে মার্চের পর ঢাকার মানুষ দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে শহর ত্যাগ করতে শুরু করে। কিন্তু এত মানুষের জন্য নিরাপদ ঠাঁই কোথায়? যখনই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কোনো শহর এলাকায় আক্রমণ করেছে, তার আগেই মানুষ শহর ত্যাগ করে পালিয়েছে। আতঙ্কিত মানুষের মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধরা ছিল। তারা ঠাঁই নেয় গ্রামে। গ্রামে যারা ছিল তারা সাদরে বরণ করে নিয়েছে সন্ত্রস্ত এই মানুষদের। এভাবে আপ্যায়নের মাধ্যমেও অনেকে যুদ্ধে অবদান রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধ তাই শুধু একতারই নয়, ত্যাগেরও বটে।
যেকোনো যুদ্ধই সংকট সৃষ্টি করে। যেমনটি আগেও বলেছি, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু মুক্তির সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে প্রেক্ষাপটকালীন পার্থক্য রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষকে তার জীবন ও অবশিষ্ট যা রয়েছে তার নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয়েছে। সংকটের এই সময়েও অনেকে উদার ও দেশাত্মবোধের উৎকৃষ্ট নজির স্থাপন করেছে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতির উদারতাও ছিল। গ্রামীণ অনেক এলাকায় পাকিস্তানিরা পৌঁছাতে পারেনি। এ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবন এমনিতেই নানা সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আর সংকটকালে এ মানুষগুলোই পালিয়ে যাওয়া মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। তাদের ঘর ছেড়ে দিয়েছে। সামান্য যা সম্বল ছিল তা দিয়েই রান্না করে খাইয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদেরও তারা আশ্রয় দিয়েছে। নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। অর্থাৎ সরাসরি বন্দুক হাতে না নিয়েও অনেকে যুদ্ধে অবদান রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের এই জাতীয় ঐক্য ও চেতনার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ডিসেম্বরে। অবশেষে মেলে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ভয়াবহ এক জনযুদ্ধে আমাদের বিজয় আসে অবশেষে।
এবার নতুন করে দেশ গড়ে তোলার পালা। তখনকার তরুণ প্রজন্ম থিয়েটারকে বেছে নিয়েছিল একটা কারণে, তখন থিয়েটারটা আমাদের কাছে আশ্রয় মনে হয়েছিল। ৩১ জানুয়ারি অস্ত্র সারেন্ডার করার পর নিজেকে উদ্বাস্তু মনে হয়েছে। আমাদের ঢাকা থিয়েটার কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদেরই দল, কাজেই নতুন দেশের ব্যাপারে আমাদের হতাশাটা একটু অন্যরকম ছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা একটা বড় ব্যাপার ছিল এবং তা খুবই ক্ষতি করেছে। থিয়েটার করা থেকে অন্য কিছুই বেশি ভাবতে হয়েছে। সেটা ১৯৭৪-’৭৫ সালের কথা বলছি। এখনও কিন্তু থিয়েটারের চেয়ে অন্য কিছু বেশি ভাবছি বলেই থিয়েটারটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক সংকট এখনও দূর হয়নি। আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের মতো সংকট ফের জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার রেখাপাত করেছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের কর্মী হিসেবে সব সময় চেয়েছি রাজনীতি থেকে সংস্কৃতিচর্চা আলাদা রাখতে। প্রগতিশীল সব শক্তির ঐক্য খুব জরুরি। আজ আমরা বিশ্বে নানাভাবে নন্দিত, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা ম্লান হতে দেওয়া যায় না। একাত্তরে যে একতা ও সহযোগিতা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দিয়েছিল, তেমন একতা এখন জরুরি।
লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব